ভূলোক
ভূলোক
অন্য গ্রহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে
পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই
সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।
পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত
হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। দুধের সর
ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার
স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে দুধের সর যেটুকু
অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে-যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা
তেমন সামান্য বলে উড়িয়ে দেবার নয়। নীচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা
হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উঁচুনিচু হতে
থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মানুষের কপালের চামড়া
কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত
পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মানুষের চামড়ার উপর বলিচিহ্নের
চেয়ে কম বৈ বেশি নয়।
প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে-যাওয়া স্তরের উঁচুনিচুতে কোথাও নামল গহ্বর, কোথাও উঠল পর্বত। গহ্বরগুলো তখনো জলে ভরতি হয় নি। কেননা তখনো পৃথিবীর তাপে
জলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হল ঠাণ্ডা, বাষ্প হল জল। সেই
জলে গহ্বর ভরে উঠে হল সমুদ্র।
পৃথিবীর অনেকখানি জলের বাষ্প তো তরল হল; কিন্তু হাওয়ার
প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই রয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাণ্ডা হলে তারা
তরল হতে পারত ততটা ঠাণ্ডায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হত
বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাপের গরমে-ঠাণ্ডায় অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি
বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিশ্বাস নিয়ে
বাঁচছি।
পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনো একেবারে থেমে যায় নি। তারই নড়নের ঠেলায়
হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নীচে থেকে কিছু সরে যায়, তা হলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, দুলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তরকে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে।
আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নীচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।
পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে যতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনো ততটা নীচে
পর্যন্ত খোঁড়া হয় নি। কয়লার খোঁজে মানুষ মাটির যতটা নীচে নেমেছে সে এক মাইলের
বেশি নয়। তাতে কেবল এই খবরটা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নীচের
দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। এই উত্তাপবৃদ্ধির
পরিমাণ সব জায়গায় সমান নয়, স্থানভেদে
মাত্রাভেদ ঘটে। এক সময়ে একটা মত চলতি ছিল যে, ভূস্তরটা ভাসছে
পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল ধাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের অস্তিত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তরে যে-সব
তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাচ্ছে তাদের থেকে। তার
অন্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত সে স্থানটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিস গলে যেতে পারে। আন্দাজ করা যাচ্ছে
সেখানকার জিনিসটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে দু’হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে-একটা খোল সে পুরু দু হাজার
মাইলের উপরে।
পৃথিবীর সমস্তটাই যদি জলময় হত তা হলে তার ওজন যতটা হত জলে স্থলে মিশিয়ে তার
চেয়ে তার ওজন সাড়ে-পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি
ঘন। তা হলে তার ভিতরে আরো বেশি ভারী জিনিস আছে ধরে নিতে হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই
তাদের ঘনত্ব বেড়ে গেছে তা নয় সেখানকার বস্তুপুঞ্জের ভার স্বভাবতই বেশি।
পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাস তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর আর যে-সব গ্যাস আছে সে অতি সামান্য। অক্সিজেন গ্যাস মিশুক
গ্যাস, লোহার সঙ্গে মিশে মর্চে ধরায়, অঙ্গারপদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জ্বালায়— এমনি করে
বায়ুমণ্ডল থেকে নিয়ত তার অনেক খরচ হতে থাকে। এ দিকে গাছপালারা বাতাসের
অঙ্গারাম্ল গ্যাসের থেকে নিজের প্রয়োজন অঙ্গার আদায় করে নিয়ে অক্সিজেন-ভাগ
বাতাসকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাসে ভরে যেত, মানুষ পেত না তার নিশ্বাসের বায়ু।
আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয় নি। যে-সব গ্যাস
মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরো অনেক উঁচুতে পৌঁছয় না। খুব সম্ভব সব চেয়ে
হালকা দুটো গ্যাস অর্থাৎ হীলিয়ম এবং হাইড্রোজেনে মিশনো সেখানকার হাওয়া।
বাতাসের ঘনত্ব কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। বাহির থেকে
পৃথিবীতে যে উল্কাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জ্বলে ওঠে, তাদের অনেকেরই এই জ্বলন প্রথম দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে তার
ঊর্ধ্বে আরো অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে তবে এই জ্বলনের অবস্থা
ঘটে।
সূর্যের আলো ৯ কোটি মাইল পেরিয়ে আসে পৃথিবীতে। গ্রহবেষ্টনকারী আকাশের শূন্যতা
পার হয়ে আসতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে
বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌঁছয় আর আঘাতে সেখানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই
ভেঙেচুরে ছারখার হয়ে যায়— কেউ আস্ত থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা
পরমাণুর যে স্তরের সৃষ্টি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় (F 2) এফ ২ স্তর।
সেখানকার খরচের পর বাকি সূর্যকিরণ নীচের ঘনতর বায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণুভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে ( F 1) এফ ১ স্তর।
আরো নীচে আরো ঘন বাতাসে সূর্যকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরো একটা যে স্তর
দেখা দেয়, তার নাম ( E) ই স্তর।
সূর্যকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উদ্যোগী।
উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকখানি নিঃস্ব হয়ে নীচের
হাওয়ায় অল্প পৌঁছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।
সূর্যকিরণ ছাড়া আরো অনেক কালাপাহাড় দূর থেকে আসে বাতাসকে অদৃশ্য গদাঘাত
করতে। যেমন উল্কা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আসে
গ্রহ-আকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের
মধ্যে তাপ জেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে সাত হাজার ফারেনহাইট
ডিগ্রি পর্যন্ত; তাতে করে বেগনি-পারের আলোর তীক্ষ্ম বাণ তূণমুক্ত হয়ে
আসে, বাতাসের অণুগুলোর গায়ে পড়ে তাদের জ্বালিয়ে চুরমার
করে দেয়। এছাড়া আর-এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে কস্মিক রশ্মি।
বিশ্বে সে-ই হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।
পৃথিবীর বাতাসে আছে অক্সিজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের কোটি কোটি অণুকণা, তাঁরা অতি দ্রুতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে
সংঘাত চলছেই। যারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে
স্বতন্ত্র ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি। সেইজন্যে পৃথিবীর বাহির আঙিনার সীমা থেকে
হাইড্রোজেনের খুচরো অণু প্রায়ই পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় দিচ্ছে। কিন্তু
দলের বাইরে অক্সিজেন নাইট্রোজেনের অণুকণার গতি কখনো ধৈর্যহারা পলাতকার বেগ পায়
না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাসে তাদের দৈন্য ঘটে নি; কেবল তরুণ বয়সে যে
হাইড্রোজেন ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।
বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাখি শুধু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেসে
বেড়ায়, বুঝতে পারি পাখিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে
বাতাসের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিসের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি
পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। সেই হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া
জিনিসের উপর প্রায় সাতাশ মণ। একজন সাধারণ মানুষের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের
উপর। তবুও তা টের পাই নে। যেমন উপর থেকে তেমনি নীচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানভাবে বাতাসের চাপ আর
ঠেলা লাগছে বলে বাতাসের ভার আমাদের পীড়া দিচ্ছে না।
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আপন আবরণে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে মহাশূন্যে প্রবল ঠাণ্ডাটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার
উড়ুনি নেই তাই সে সূর্যের তাপে ফুটন্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময়
যখনই পৃথিবী চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাওয়া
থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদের কেবল এইমাত্র ত্রুটি নয়, বাতাস নেই বলে সে একেবারে বোবা, কোথাও একটু শব্দ
হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাসে নানা আয়তনের সূক্ষ্ম ঢেউ ওঠে, সেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেই-সব ঢেউ নানারকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে সাড়া দিতে থাকে। আরো একটি
কাজ আছে বাতাসের। কোনো কারণে রৌদ্র যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেষ্ট
আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়তে
কেবল সেইখানেই আলো হত। ছায়া বলে কিছুই থাকত না। তীব্র আলোর ঠিক পাশেই থাকত ঘোর
অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্দুর উঠত চোখ রাঙিয়ে আর তার তলা হত মিশমিশে কালো, ঘরের ছাদে ঝাঁ ঝাঁ করত দুইপহরে রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত
দুইপহরের অমাবস্যার রাত্রি। প্রদীপ জ্বালার কথা চিন্তা করাই হত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে সব-কিছু জ্বলে।
গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে
ক্লোরোফিল বলে একটি পদার্থ আছে— তারাই সূর্যের আলো
জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। তাদের শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে ফলে-ফসলে আমাদের
খাদ্য, আর গাছের ডালাতে গুঁড়ির কাঠ। পৃথিবীর বাতাসে আছে
অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামান্য পরিমাণে। উদ্ভিদবস্তুতে যত অঙ্গার পদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী-আঙ্গারিক
গ্যাস মানুষের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের
করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লোরোফিলের যোগে এই অক্সিজেনী
আঙ্গারিককেও জলে এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে।গাছের থেকে আমরা নিই ধার করে। পৃথিবীতে সমস্ত জন্তুরা মিলে যে
অক্সিজেন-মিশ্রিত আঙ্গারিক বাষ্প নিশ্বাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা লাগে গাছপালার
প্রয়োজনে। আগুন-জ্বালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তুদেহের
পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারখানায় রান্নার কাজে
কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকে উদ্ভব হয় বহু কোটি মণ
অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস। গাছের পক্ষে যে হাওয়ার ভোজের দরকার সেটা এমনি করে জুটতে
থাকে ত্যাজ্য পদার্থ থেকে।
বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস।
তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলে নি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইট্রোজেন।
কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র অক্সিজেনে আমাদের
প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই
বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।
সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে স্যাঁতসেঁতে। যে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।
উপরকার বায়ুমণ্ডলে ভাঙা পরমাণুর বৈদ্যুতস্তরের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া
সহজ বাতাসের দুটো স্তর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে তার
বৈজ্ঞানিক নাম ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere), বাংলায় একে
ক্ষুব্ধস্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের
মাপে এই ক্ষুব্ধস্তরের উচ্চতা খুবই কম, কিন্তু এইটুকুর
মধ্যেই আছে বাতাসের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এ স্তর
অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গায়ে লেগে আছে বলে এই স্তরে সর্বদা পৃথিবীর
উত্তাপের ছোঁয়াচ লাগে। সেই উত্তাপের কমায়-বাড়ায় হাওয়া ক্রমাগত ছুটোছুটি করে।
এই স্তরেই তাই ঝড়বৃষ্টি। এর আরো উপরে যে স্তর পৃথিবীর তাপ সেখানে ঝড়তুফান চালান
করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ স্তরের নাম দিয়েছেন
স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere), বাংলায় আমরা বলব
স্তব্ধস্তর।
আদি সূর্য থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাষ্পদেহী আদিম পৃথিবী থেকে
বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বৎসরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, চাঁদও হল তাই।
২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭ ১/৩ দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ
করছে। সেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস
প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩ ১/২ গুণ ভারী। অন্যান্য
গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম বলে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে
এত বড়ো দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। দুরবীনে
চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে ঐ তৈরি। ওর উপরে আছে
বড়ো বড়ো গহ্বর আর বড়ো বড়ো পাহাড়।
পৃথিবীর টানে চন্দ্র পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু
কম লাগে। গড়পড়তায় তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে আধ মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে
সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সমানই লাগে।
তার দিন আর বৎসর চলে একই রকম ধীর মন্দ চালে।
চাঁদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গতিবেগ যদি সেখানে সেকেণ্ডে
১ ১/২ মাইল হয় তা হলে চাঁদের টান অগ্রাহ্য করে তা ছুটে বাইরে যেতে পারে। চাঁদ যে
নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম
হয়ে ওঠাতে চাঁদ তার বাতাসের অণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতড়ি বাষ্প
হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের অণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন
ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে
পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তালপাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।
রাতের বেলায় যাদের আমরা খসে-পড়া তারা বলি সেগুলো যে তারা নয় তা আজ আর কাউকে
বলতে হবে না। সেই উল্কাপিণ্ডগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর
উপর। তার অধিকাংশই বাতাসের ঘেঁষ লেগে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্চে। যেগুলো বড়ো
আয়তনের, তারা জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পৌঁছয়, বোমার মতো যায় ফেটে, চার দিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।
চাঁদেও ক্রমাগত এই উল্কাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু
হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে চাঁদের সর্বাঙ্গে। বেগ কম নয়, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল, সুতরাং ঘা মারে
সর্বনেশে জোরে।
চাঁদে বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। যে গলন্তপদার্থ
ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এতযুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে
পারে নি। ছাইঢাকা আছে বলে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নীচে যেতে পারে না, আর নীচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।
চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাণ্ডা যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০
ফারেন্হাইট ডিগ্রি নীচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের
উপরে পড়ে তখন তার উত্তাপ কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রি ফারেন্হাইট কমে
যায়।
হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় সূর্যের আলো নীচে প্রবেশ করতে পারে না
বলে সঞ্চিত কোনো উত্তাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি
এর উত্তাপ কমে আসে। এ-সব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আগ্নেয়গিরির ছাই
ঢেকে রেখেছে চাঁদের প্রায় সব জায়গা।
চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর
সমুদ্রগুলোতে, সেখানে জোয়ারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরের জ্বরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের
রোগীরা ভয় করে অমাবস্যা পূর্ণিমাকে।
আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সত্তর-আশি কোটি বছর ধরে
চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত; কোথাও অগ্নিগিরি
ফুঁসছে তপ্ত বাষ্প। উগরে দিচ্ছে তরল ধাতু, ফোয়ারা ছোটাচ্ছে
গরম জলের। নীচের থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়পর্বত, তলিয়ে যাচ্ছে ভূখণ্ড।
পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়শো কোটি বছর যখন পার হল অশান্ত আদিযুগের
মাথা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে সৃষ্টির সকলের চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা দেখা
দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমশ মনের উদ্ভব হল তার ঠিকানা
পাওয়া যায় না। তার আগে পৃথিবীতে সৃষ্টির কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল
প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট
করে জোড়াতাড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমুদ্রের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই
বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন।
এদের পূর্ববর্তী পদার্থরাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।
নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ নীহারিকায়, তেমনি পৃথিবীতে
জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম
অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো
অঙ্গবিভাগহীন – তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম
দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্ল্যাজ্ম্। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাষ্পে, তেমনি বহু যুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর
নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা— আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে
দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষু হাত পা
নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ
করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়েই টেনে নেয়। পাকযন্ত্র
বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমস্ত দেহটাকে ভাগ করে তার বংশবৃদ্ধি হয়। এই
অমীবারই আর-এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারি
দিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি সূক্ষ্ম
দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জমে জমে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি
হয়েছে।
বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি
অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অতিসূক্ষ্ম জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ
এবং স্বতন্ত্র, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি
আছে যাতে করে বাইরে থেকে খাদ্য নিয়ে নিজেকে পুষ্ট, অনাবশ্যককে ত্যাগ ও
নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বহুগুণিত করার শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে।
এই জীবাণুকোষ প্রাণলোকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত
সংঘবদ্ধ হতে থাকল ততই জীবজগতে উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগল। যেমন বহুকোটি তারার
সমবায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোষের সমাবেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর
দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ সৃষ্টি করে নূতন নূতন রূপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে
চলেছে। আমরা এত কাল নক্ষত্রলোক সূর্যলোকের কথা আলোচনা করে এসেছি। তার চেয়ে বহুগুণ
বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শান্ত করে দিয়ে ক্ষুদ্রায়তন গ্রহরূপে
পৃথিবী যে অনতি-ক্ষুব্ধ পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মন-এর
আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে এ কথা যখন চিন্তা করি তখন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই
পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু এ
কথা মানতে মন চায় না, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক
অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে— যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।



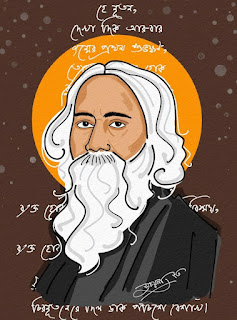
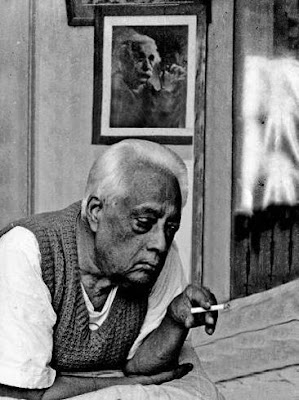
মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন