উপসংহার
উপসংহার
একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহুকোটি বৎসর পূর্বে তরুণ
পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে
এনেছি কত গোপনে। দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টিকার্য নব নব পরীক্ষার
ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে। যোজনা করবার, শোধন করবার, অতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বুদ্ধি প্রচ্ছন্নভাবে তাদের মধ্যে
কোথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নিজেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না।
অতি-পেলববেদনাশীল জীবকোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথাযথ পথে সমষ্টি বাঁধছে জীবদেহে, নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে; নিজের ভিতরকার উদ্যমে জানি না কী করে দেহক্রিয়ার এমন
আশ্চর্য কর্তব্যবিভাগ করছে। যে কোষ পাকযন্ত্রের, তার কাজ এক রকমের, যে কোষ মস্তিষ্কের, তার কাজ একেবারেই অন্য রকমের। অথচ জীবাণুকোষগুলি মূলে
একই। এদের দুরূহ কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা হল কোন্ হুকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের
মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য নামে একটা সামঞ্জস্য সাধন করল কিসে। জীবাণুকোষের দুটি
প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে খাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অনুরূপ জীবনকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও
বংশরক্ষার জটিল প্রয়াস গোড়াতেই এদের উপর ভর করল কোথা থেকে।
অপ্রাণ বিশ্বে যে-সব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা। মন এই-সব
ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথায়। পাথর
লোহা গ্যাসে নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেই। এই দুঃসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ
একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে— অতিক্ষুদ্র
জীবকোষকে বাহন করে।
পৃথিবীর সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকল-কিছুর সঙ্গে
সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বুদ্ধি মানতে চায় না। আমরা
জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা
জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে
যে-সকল স্থুল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে
প্রচ্ছন্ন-আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ
প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি
ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে
চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই
মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি
সৃষ্টির শেষ পরিণাম।
পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্ষয় হচ্ছে এ কথা চাপা
দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপ নিয়ে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই
হচ্ছে যে খরচ হতে হতে ক্রমশই নেমে যায় তার উষ্মা। সূর্যের উপরিতলের স্তরে যে
তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শূণ্য ডিগ্রির উপরে ছয় হাজার সেন্টিগ্রেড। তারই
কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উদ্যমে জীবজন্তু চলাফেরা করছে। সঞ্চয় তো ফুরোচ্ছে, একদিন তাপের শক্তি মহাশূণ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এনে রূপ
দেবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারি দিকের সঙ্গে
একাকার হয়ে যখন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীবযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না।
জগতে যা ঘটছে, যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে
আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত, সমস্তই তো বিশ্বের
হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্ক ফেলে চলেছে। সে সময়টা যত দূরেই হোক একদিন বিশ্বের
নিত্যখরচের তহবিল থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শূণ্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী
গণিতবেত্তা বিশ্বের মৃত্যুকালের গণনায় বসেছিল।
আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র
প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে
থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি এ একান্ত অন্তের
অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে,ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।
সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা ঘূর্ণিটানের আবর্তে ধরা পড়ে একই দিকে চঞ্চলে সূর্যপ্রদক্ষিণের পালা শেষ
করছে। সৃষ্টির গোড়ার কথা যাঁরা ভেবেছেন তাঁরা এতগুলি তথ্যের মিলকে আকস্মিক বলে মেনে
নিতে পারেন নি। যে মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার সুস্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে
তা-ই প্রাধান্য পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। যে-সব বস্তুসংঘ নিয়ে সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি
তাদের ঘুর্ণিবেগের মাত্রার হিসাব একটা প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-সব
মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। হিসাবের গরমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই
মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে।ঘূর্ণিবেগের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে দু-একটি মতবাদ
এত কাল টিঁকে ছিল তাদের বিরুদ্ধেও নূতন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে। আমেরিকার প্রিন্স্টন
বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ডিরেক্টর হেন্রি নরিস রাসেল সম্প্রতি জীন্স ও লিট্ল্টনের
মতবাদের যে বিরুদ্ধসমালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায়
নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী
বাতিল-করাদের পাশেই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রদের সংঘাতে গ্রহ-লোকের সৃষ্টি হলে
জ্বলন্ত গ্যাসের যে টানাসূত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হত যে এই
বাষ্পপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু অতিদ্রুত তাপ ছড়িয়ে
দিয়ে এই টানাসূত্র ঠাণ্ডা হয়ে একটা স্থিতি পেতে চাইত; এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়ায়, মুক্তি আর বন্ধনের
টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই হেনরি রাসেল আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে
দুর্বোধ্য গণিতশাস্ত্রের হিসাব থেকে মোটামুটি প্রমাণ হয়েছে যে টানাসূত্রের
প্রত্যেকটি পরমাণু তেজের প্রবল অভিঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশূণ্যে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যে বাধার কথা তিনি
আলোচনা করেছেন তা জীন্স ও লিট্ল্টনের প্রচলিত মতবাদের মূলে এসে কঠোর আঘাত করে
তাদের আজ ধূলিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।



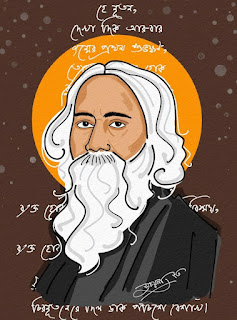

মন্তব্যসমূহ
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন